

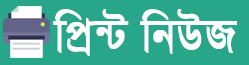
কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন উপলক্ষে আমার কিছু কথা কিছু লেখা- উপস্থাপন করছিঃ জীবনানন্দ, তুমি এক রাত্রির নীরব সঙ্গী, শীতল বাতাসের মতো এসে ছুঁয়ে গেছো হৃদয়। বনানী, ফুল আর নদী তোমার কবিতায় সঙ্গী,
তুমি বলেছো, জীবনের খোঁজ মিলবে নিঃসীম অন্ধকারে।
আজ ১২৬ বছর পর, তোমার কবিতার আলো
রয়েছে আমাদের মাঝে, চিরকাল, চিরন্তন।
অগণিত শব্দ, রূপে, অক্ষরে তোমার সৃষ্টি,
আজও বাঁচিয়ে রেখেছে তোমাকে আমাদের স্মৃতিতে।
তোমার লেখা সেই নিঃশব্দ আকাশে,
যেখানে বিরহের গান বেজে উঠে, কখনো শান্ত, কখনো তীব্র।
আমরা মনে রেখেছি তোমার প্রতিটি চরণের ধ্বনি,
আমাদের হৃদয়ে আজও তুমি জীবন্ত, চিরকালীন।
কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর জন্ম বা মৃত্যু নিয়ে সরাসরি কোনো কবিতা লিখে থাকেননি। তবে, তাঁর কবিতার মধ্যে জীবনের অন্তর্নিহিত বিষণ্ণতা, মৃত্যুর অনিশ্চয়তা, এবং অস্তিত্বের সঙ্গতি নিয়ে অনেক নান্দনিক ও গভীর ভাবনা রয়েছে। তাঁর কবিতার মধ্যে অনেক সময় মৃত্যু এবং জীবনের অর্থ নিয়ে আক্ষেপ বা ধোঁয়াশা দেখা যায়।
বিশেষভাবে, তাঁর বিখ্যাত কবিতা “বনলতা সেন”-এ জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুর সন্নিকটে আসার ভাবনা ও জীবনের অন্তিম মুহূর্তের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন, যদিও এটি সরাসরি মৃত্যু বা জন্মের প্রসঙ্গ নয়, তবে জীবনের অন্তর্নিহিত ধারার প্রতি তাঁর এক গভীর দৃষ্টি প্রকাশ পায়।
“বনলতা সেন” কবিতার একটি অংশ:
“যখন রাতের রাশিরা কাঁপে ভরা আকাশে
একটি তারা, দুটি তারা — সমস্ত রাত।
তখন তুমি আসো, এসো! বসে পড়ো নিঃশব্দে
আর চোখে চোখে বলো— ‘সাথে চল, কোথাও।’
এই কবিতায় কবি এক গভীর শূন্যতা এবং অনন্ত জীবনের অজ্ঞতা এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া আত্মিক এক যাত্রা তুলে ধরেছেন। বনলতা সেন তাঁর কবিতায় এক প্রকার স্মৃতি বা চিরকালীন আশ্রয় হয়ে ওঠে, যা জীবনানন্দের জীবন-মৃত্যু ভাবনা থেকে এক ধরণের মুক্তি বা শান্তি খুঁজে পায়। তবে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যে মৃতু ও জন্মের বিষয়ের দিকে একটি নীরব নজর দেওয়া হয়, তা তাঁর কবিতার জ্যোতির্ময়তা এবং বিমূর্ততার মধ্যে নিহিত।
“কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন,” তাদের মধ্যে কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি তাঁর বিশেষ সম্মান ছিল। যদিও নজরুলের অধিকাংশ কবিতা সাম্প্রতিক বিষয়ক ও জাতীয়তাবাদী ছিল, তবুও তিনি জীবনানন্দ দাশের রচনা ও সাহিত্যকর্মকে গভীরভাবে সম্মান করতেন।
নজরুলের কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ দাশের প্রতি সরাসরি বা বিশেষ কোনো রচনা না থাকলেও, তাঁর কিছু লেখার মধ্যে জীবনানন্দের সাহিত্যিক প্রভাবের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। বিশেষত, কবি নজরুলের “কবিতা” (Kobita) নামক কবিতাটি, যা কবিতার মহিমা এবং কবির ভাবনা নিয়ে লেখা হয়েছে, তাতে জীবনানন্দের সাহিত্যকর্মের প্রতি একটি অঘোষিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।
কবিতা:
“কবিতা তোমার তরণী, হে! চিরকাল,
নদী, পাহাড়, হাওয়া, ভোরের আকাশে।
যতই তুমিই বর্বর হও,
ততই তোমায় সে শিখিয়ে যাবে,
ধৈর্যের আঁচল, শান্তির তরণী।”
এতে কবি নজরুল কবিতার গভীরতা ও তার মানবিক উপস্থাপন নিয়ে কিছু ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, যা জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়। জীবনানন্দের স্বপ্নময় ও নৈরাশ্যবাদী কবিতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নিস্তব্ধতা নিয়ে গভীর ভাবনা, নজরুলের কবিতায় একটা অদৃশ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করে।
এছাড়া, “বিদ্রোহী” কবিতায় কবি নজরুল দুঃখ-যন্ত্রণা ও সংগ্রামের কথা বলেছেন, যা জীবনানন্দ দাশের অন্তর্মুখী কবিতার বিপরীতে এক শক্তিশালী, উদ্দীপক বার্তা পাঠায়।
জীবনানন্দের কবিতায় নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতা যেমন দেখা যায়, তেমনই নজরুল তাঁর কবিতায় সংগ্রাম, প্রতিরোধ এবং বীরত্বের কথা বলেছেন। এই দুই কবির মধ্যে একধরনের বিপরীতমুখী, তবে গভীর সম্মানজনক সম্পর্ক বিদ্যমান।
জীবনে প্রথম প্রথম যখন প্রেম করতাম, তখন নিজেকে কবি কবি ভাবতাম, কবি জীবনানন্দের কবিতার পংক্তি কয়েক লাইন শিখে প্রেম পত্র লিখতাম, তখন কিন্তু এই কবির কবিতার কথার গভীরতা বুঝতে পারিনি, পরেতো- জীবনে বাংলায় কোন কবিও কবিতার কথা আসলেই কবি জীবনানন্দের কথা আগেই বলতাম। লেখা লেখিতে এসে কবি জীবনানন্দের কবিতার সাথী হওয়ার চেষ্টা করেছি।
১৭ ই ফেব্রুয়ারী কবির ১২৬তম জন্নদিন,এই মহান কবি-র প্রতি শ্রদ্বা জানিয়ে আমি কিছু লিখার চেষ্টা করছি। তবে কবিকে নিয়ে বেশি কিছু লিখার শব্দ জ্ঞান আমার নেই। তবুও কবির প্রতি ভালোবাসার বহীপ্রকাশ আজকের এই লেখা। আগামী
২২ শে অক্টোবর কবির প্রয়ান দিবসে বিস্তারিত লেখা লিখবো বলে আশা করছি আপাততঃ এই
লেখাটি কবির কিছু কবিতার -পংক্তি মালা দিয়ে শুরু করছি-
অনেক মুহূর্ত আমি করেছি ক্ষয়, ক্ষয় করে ফেলে বুঝেছি সময় যদিও অনন্ত, তবু প্রেম যেন অনন্ত নিয়ে নয়।
কবি অন্য এজটি কবিতায় লিখেছেন — মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ হয়ে গেলে রয়ে যায় চারি দিক ঘিরে এই দেশ।
নদী, মাঠ,পাখিদের ওড়না ভার ওড়া ভার গাছের শিয়রে
কমন রঙের ঢেউয়ে এসে
কিছুক্ষণ খেলা করে।
–ভোর হয়,
কেযেন আমাকে দিতে চায়
শেষরাত–
কোন আড়া, শেষরাত আমাকে দিতে চায় তার ভোর হয়ে ওঠার।
কবি জীবনানন্দের কবিতার পংক্তি মালার দিয়ে হাজরো বছর লেখা যাবে তবুও শেষ হবেনা।
আধুনিক কাব্যকলার বিচিত্র ইজম প্রয়োগ ও শব্দ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ও তার অনন্যতা বিষ্ময়কর। বিশেষতঃ কবিতার উপমা প্রয়োগে জীবননান্দের নৈপুন্য তুলনাহীন। কবিতাকে তিনি মুক্ত আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করে গদ্যের স্পন্দনযুক্ত করেন, যা’ পরবর্তী কবিদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। জীবন বোধকে নাড়া দিয়েছে।
কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও সমাজ সেবক । তিনি ‘ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মাতা কুসুম কুমারী ছিল একজন বিখ্যাত কবি। জীবনানন্দ দাশের বাল্য শিক্ষার সূত্রপাত হয় মায়ের কাছেই। তারপর তিনি বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন জীবনানন্দ দাশ। ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। ১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। জীবনানন্দ দাস ১৯৩৫ সালে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছু আগে তিনি স্বপরিবারে কলকাতায় চলে যান।
জীবনানন্দের কাব্যচর্চার শুরু হয় অল্প বয়স থেকেই। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তার প্রথম কবিতা ‘বর্ষ-আবাহন’ ব্যহ্মবাদী পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২৬/এপ্রিল ১৯১৯খ্রি:) প্রকাশিত হয়।
১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রস্থ ‘ঝরাপালক’। ১৯৩০ সালের ৯ মে বিয়ে করেন রোহিনী কুমার গুপ্তের মেয়ে লাবণ্য গুপ্তকে। বিবাহিত জীবন তার মোটেই সুখের ছিল না। বিয়ের পর অনেকদিন কর্মহীন জীবন কেটেছে জীবনানন্দ দাশের। দুটি সন্তান ছিল তার মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও ছেলে সমরানন্দ। জীবননান্দ দাশ বৈষয়িক জীবনে কখনো সফলতা পাননি । বার বার ভাবতেন আত্মহত্যার কথা। ভেবেছিলেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সাগরের জলে ডুবে মরবেন।। সারাটা জীবন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মনে করতেন আমাদের এই বাংলাদেশকে। জীবননান্দ দাশ কবি হলেও অসংখ্য ছোটগল্প, কয়েকটি উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি এগুলো প্রকাশ করেননি। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে জীবনানন্দের স্বতন্ত্র প্রতিভা ও নিভৃত সাধনার উন্মোচন ঘটে মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত তার অসংখ্য পান্ডুলিপিতে। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যে নজরুল, সতেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্য ধারার প্রভাব থাকলেও দ্বিতীয় কাব্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন মৌলিক ও ভিন্ন পথের অনুসন্ধানী।
তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে ধূসর পান্ডুলিপি (১৯৩৬ খ্রি:), বনলতা সেন (১৯৪২ খ্রি:), মহাপৃথিবী (১৯৪৪ খ্রি:), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮ খ্রি:), রূপসী বাংলা (১৯৫৭ খ্রি:), বেলা অবেলা কার বেলা (১৯৬১ খ্রি:)। এছাড়াও বহু অগ্রন্থিত কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে মাল্যবান (১৯৭৩ খ্রি.), সুতীর্থ (১৯৭৭ খ্রি.) জলপাইহাটি (১৯৮৫ খ্রি.) জীবন প্রণালী (অপ্রকাশিত), রাসমতির উপাখ্যান (অপ্রকাশিত) ইত্যাদি। তার রচিত গল্পের সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। কবিতার কথা (১৯৫৫ খ্রি.) নামে তার একটি মননশীল ও নন্দন ভাবনা মূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে তার গদ্য রচনা ও অপ্রকাশিত কবিতার সংকলন রূপে ‘জীবনানন্দ সমগ্র’ (১৯৮৫ খ্রি:) নামে বারো খ- রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি:) নিবিড় প্রকৃতিচেতনা তার কবিতায় গভীর দ্যোতনা লাভ করেছে। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা- পুরাণের জগৎ তার কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্র রূপময়। বিশেষত ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে যেভাবে আবহমান বাংলার চিত্ররূপ ও অনুসুক্ষè সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি রূপসী বাংলার কবি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন।
জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তার কবিতার চিত্রময়তা, যার সঙ্গে আমরা অনায়েসে ঘনিষ্ঠ বোধ করি। এটি তার জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারণ। যে প্রকৃতির বর্ণনা জীবনানন্দ করেন, বাস্তবে তাকে আমরা আর খুঁজে পাই না। পাই না বলেই হয়তো হারানো সেই সৌন্দর্যকে আমরা নিজের ভেবে আরও প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরি। অনেক সময় তার উচ্চারিত শব্দ চিত্র আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়েগেছে। স¤্রাট বিম্বিসার কে, বির্দভ নগর কোথায়,তা’না জেনেই মনে মনে নিজের মতো এক চিত্র ও ধ্বনির জগৎ আমরা গড়ে নেই। আগাগোড়া তার কবিতার সুর বিষন্ন, সবচেয়ে উজ্জ্বল যে রং তাও ধূসর, অথচ তা’ সত্ত্বেও জীবননান্দ দাশের কবিতায় আমরা ব্যক্তিগত প্রণোদনার উৎস খুঁজে পাই। তবে প্রকৃতির পাশাপাশি জীবনানন্দের শিল্প জগতে মূর্ত হয়েছে, বিপন্ন মানবতার ছবি এবং আধুনিক নগর জীবনের অবক্ষয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও সংশয়, রোধে জীবনানন্দ ছিলেন একজন সমাজ সচেতন কবি। তিনি ইতহাস চেতনা দিয়ে অতীত ও বর্তমানকে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সূত্রে বেঁধেছেন। তার কবি স্বভাব ছিল অন্তর্মুখী, দৃষ্টিতে ছিল চেতনা থেকে নিশ্চেতনা ও পরচেতনার শব্দ রূপ আবিষ্কারের লক্ষ্য। এ সূত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন ইম্প্রেশনিস্টিক রীতি, পরাবাস্তবতা, ইন্দীয় বিপর্যাস ও রঙের অত্যাশ্চর্য টেকনিক। জীবনানন্দ বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে অজ্ঞাত পূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছিলেন তা জীবনানন্দের সমকালীন সময়ে খুব কম কাব্য রসিক কিংবা নন্দন তাত্ত্বিকরা বুঝতে পেরেছিলেন।
জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে দাম্পত্য জীবনের সঙ্কট, নরনারীর মনস্তত্ত্ব ও যৌন সম্পর্কের জটিলতা এবং সমকালের আর্থসামাজিক কাঠামোর বিপর্যয়। তার প্রায় গল্প উপন্যাস আত্মজৈবনিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জীবনান্দের কবিতার ভূমিকা ঐতিহাসিক। ষাটের দশকে বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় বাঙালি জনতাকে তার “রূপসী বাংলা” তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করে। জীবনানন্দ ছিলেন আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তার বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ “বনলতা সেন” নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে ১৯৫৩ সালে পুরস্কৃত হয়। জীবনানন্দের “শ্রেষ্ঠ কবিতা” গ্রন্থটি ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জীবনানন্দ দাশ অকালে মৃত্যুবরণ করেন।
জীবনানন্দ দাসকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ ও বিস্ময় প্রায় অন্তহীন। তার ব্যবহৃত শব্দের ভেতর থেকে ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত অনুভূতির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সেই সব শব্দ থেকে বিচ্ছুরিত হয় একই সাথে আলো আর অন্ধকার।
বিশ শতকের অন্য কোনো বাঙালি কবি আমাদের কল্পনায় এমন প্রবলভাবে দাগ কাটেনি। আজও তার কবিতার অলঙ্কার শব্দ ব্যবহার এবং অধুনা আবিষ্কৃত গদ্যের ভাষা আমাদের ক্রমেই বিস্মিত করে চলেছে। কবি’র শেষ সময়ে কিছু টুকিটাকি কথা না বল্লেই হবেনা। আমি লেখা শুরুতেই বলেছি
কবি জীবনানন্দ দাশ (জন্ম: ১৭ ফেব্রæয়ারি ১৮৯৯, মৃত্যু: ২২ অক্টোবর ১৯৫৪) ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর কবি। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই লাজুক। আত্মভোলা ধরনের। অসম্ভব পড়ুয়া। ভালোবাসতেন একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা। এমন একটা সময় ছিল যখন রোজ রোজ পাঁচ/ সাত মাইল হাঁটতেন। তাঁর বেশ পছন্দ ছিল হাঁটাহাঁটি। কলকাতায় পড়ন্ত দুপুরে যখন বাড়ি থেকে বেরুতেন, রাস্তা থাকতো জনবিরল। প্রখর রোদে এলোমেলো একা একা ঘুরে বেড়াতেন। বন্ধু সুবোধ রায়ের সঙ্গে কবি একদিন গেছেন আচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে যথারীতি ট্রাম-বাস নয়, হেঁটে। এই ফাঁকে কবির মৃত্যুপরবর্তী সময়ে সুবোধ রায়ের স্মৃতিচারণের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিই আমরা।
সুবোধ রায় লিখেছেন,
সন্তর্পণে অতিক্রম করলাম চৌরঙ্গীর মসৃণ পীচের রাস্তা। তারপর ধু ধু গড়ের মাঠ। তমসাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ শ্যামলিমা। ঘাস পেলে জীবনানন্দ আর কিছু চান না। সবুজের প্রতি এক আশ্চর্য অনুরক্তি আর আকর্ষণ। সাপের যেমন বাঁশি, হাঁসের যেমন জল, পাখির যেমন মুক্ত আকাশ। মনে পড়ে কবির অবিস্মরণীয় কবিতাকেঃ
রয়েছি সবুজ মাঠে–ঘাসে–
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এইসব ছুঁয়ে
ছেনে! সে এক বিস্ময়।
প্রতিদিন সাদার্ন য়্যাভিনু দিয়ে হাঁটতেও এর পরিচয় পেয়েছি বারবার। ঘাসপথ চাই-ই চাই। ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদিই-বা নামালাম রাস্তায়–কখন দেখি ঠিক উঠে পড়েছেন ঘাসে! এই পরীক্ষা কতোবার কতোভাবে করেছি। ব্যর্থ হয়েছি বারবার।
…হাঁটায় ক্লান্তি নেই জীবনানন্দের। যদি বলেছি কোনোদিন আর পারছিনে, দাঁড়াই একটু, অমনি কপট ভর্ৎসনার গর্জন শুনতে হয়,‘খাড়ান কিয়া’ প্রশ্ন করি, ‘এ আবার কোন দেশী ভাষা?’ উত্তর হয়, ‘বরিশালের। অরবিন্দ গুহকে জিজ্ঞেস করবেন।’ দ্বিরুক্তি না ক’রে হেঁটে চলেছি। জনহীন পথ। হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন কবি,‘ভাউয়া–ভাউয়া’। ‘সে আবার কী?’ ‘ঐ যে তাকিয়ে আছে। ভীষণ লাফায় আর নাকি চোখ খুবলে নেয়।’ ‘তা ভাউয়া ভাউয়া ক’রে চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? ও তো কোলাব্যাং।’ ‘বরিশালে ভাউয়া বলে। অরবিন্দ গুহকে জিজ্ঞেস করবেন।” রাখতেন। আমার ছোটভাই বিছানায় বাবার পায়ের কাছে বসে গল্প করত। একবার আমায় বললেন, ‘তোর বইয়ের লিস্ট দে, কিনে দেব। ভাল করে পড়ছিস তো? ফার্স্ট ক্লাস পেতে হ’লে কিন্তু ভাল করে পড়তে হয়।’একদিন ছিল ভিজে মেঘের দুপুর। নীলাঞ্জন আভায় বাবা লিখছেন। বললাম বাবা কালিদাসের মেঘদূত বড় সুন্দর না? মৃদু হেসে মেঘদূতের প্রথম কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন তিনি। কী মেঘের মত স্বর, কী সুন্দর উচ্চারণ।
বাবা ছিলেন এক তাপস। পান সিগারেট কখনো খেতে দেখিনি। সিনেমা দেখলেও হয়তো এক বছর পর। খেতে খুব ভালবাসতেন।
সন্ধ্যা বেলায় বাবা রাসবিহারী সাদার্ন এভেনিউ দিয়ে সামান্য হেঁটে আসতেন। আমাদের বরিশালে ছিল অফুরান গাছ গাছালি চমৎকার বাগান সবুজ মাঠ। সেই মস্ত মাঠে ছিল সবুজ ঘাস। শিশিরের স্বাদ। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের সন্ধ্যের মত সন্ধ্যা আমরা বরিশালে দেখেছি। সেই হারানো কথা মনে রেখে হয়তো সন্ধ্যায় সামান্য হাঁটতেন।
এমনি এক সন্ধ্যা বেলায় পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে কবি আর ঘরে ফিরলেন না। শুনলাম ট্রাম এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমরা দৌড়ে গেলাম শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। দেখি, বাবার মলিন কাপড়ে রক্তের দাগ।
দু’দিন পরে ডাক্তারের হাত ধরে বলেছিলেন, ‘ডাক্তারবাবু, আমি বাঁচবো তো?’
বাবার শরীরের অনেক হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হাসপাতালে হাজারো মানুষ আসতেন। শুভার্থী সুহৃদস্বজন। হাতে ফল, কণ্ঠে শুভেচ্ছা। হাসপাতালে সেবিকা ছিলেন। বাবাকে দেখতেন। তবুও কজন আত্মীয়, দু-তিন জন তরুণ কবি ও আমরা–সব সময় কাছে থাকতাম, পরিচর্যার জন্য।
একদিন বাবার শিয়রে বসে আছি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। দেখলাম বাবার চোখ সজল। যে মানুষ কখনো ভেঙে পড়েননি, আজ সময়ের নির্মম আঘাতে সে চোখ সজল। আমি সামনে এলাম। আমায় দেখতে পেয়ে বাবা নিমেষে সহজ হলেন। বললেন, অমুক পত্র পত্রিকা এনে রাখিস।
হাসপাতালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চেয়েছিলেন। শেষদিকে ডাক্তার বিধান রায় দেখতে এলেন। ডাক্তার রায় খানিকক্ষণ বাবার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না। শুধু বাবার জন্যে অনেক সুব্যবস্থা করে গেলেন। কিন্তু জীবনকে জানবার অবিরাম ভার বাবাকে আর বইতে হল না।সেটা ১৯৫৪-এর ২২ অক্টোবর। রাত প্রায় সাড়ে এগার। আমার সবচেয়ে প্রিয়জনের সবচেয়ে ধূসর সময়।
বাবা সজোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন। বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সবাই। অনেক স্বজন– ক্রমে জীবনের স্পন্দন থেমে গেল।”
এই বিধান রায় ছিলেন নামজাদা ডাক্তার, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী।
কবি জীবনানন্দ দাশ কবি নজরুল ইসলামকে সরাসরি কোনো কবিতা বা লেখায় উল্লেখ করেছেন বলে ইতিহাসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্মের মধ্যে কবি নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান ছিল, এটি তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য এবং লেখার মাধ্যমে বোঝা যায়।
কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় সরাসরি নজরুলের নাম না নিলেও, নজরুলের সাহিত্যের প্রতি তাঁর সম্মান ছিল। অনেকের মতে, জীবনানন্দ দাশ কবি নজরুলকে একজন শক্তিশালী কবি হিসেবে মনে করতেন এবং তাঁর সাহিত্যকর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করতেন।
তবে, এমন একটি কবিতা বা লেখা পাওয়া যায় না যেখানে জীবনানন্দ দাশ সরাসরি কবি নজরুল ইসলামের প্রতি কোনো উল্লেখ করেছেন। এটি সম্ভবত যুগের পার্থক্য এবং ব্যক্তিগত মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে হতে পারে। তবে উভয় কবি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, এবং তাঁদের সাহিত্য একে অপরকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে।
লেখকঃসাংবাদিক, গবেষক, সাহিত্যিক,টেলিভিশন উপস্থাপক ও মহাসচিব, চট্টগ্রাম নাগরিক ফোরাম।
email Kamaluddin 2247@gamal.com