

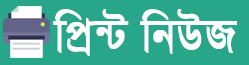
বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা একসময় ছিল ন্যায় ও সত্যের পথে অবিচল থাকার অঙ্গীকার। কিন্তু আজ তা যেন পরিণত হয়েছে ভিন্ন এক বাস্তবতায়—যেখানে সত্য চাপা পড়ে, প্রশ্নবিদ্ধ হয় ন্যায়বিচার, আর রাষ্ট্র যেন নির্যাতনের মঞ্চে পরিণত হয়। প্রায় তিন দশক ধরে লেখালেখির অভিজ্ঞতা এবং ২৮টিরও বেশি দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা কেমন হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে সাংবাদিকতার সেই নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের অভাব আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো। এই ব্যথা থেকেই আজকের লেখার সূত্রপাত। ধর্ষণ একটি ভয়াবহ অপরাধ, যা শুধু ব্যক্তি বিশেষের ওপর আঘাত নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতিরও প্রতিফলন। কিন্তু যখন গণমাধ্যম এই সংবাদের বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল উপস্থাপনার পরিবর্তে অনৈতিক ও অসংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তখন তা ভুক্তভোগীর জন্য নতুন করে মানসিক নির্যাতনের সৃষ্টি করে।
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের গাফিলতি, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও পেশাগত অসচেতনতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়ই আমরা দেখি, ধর্ষণের শিকার ভিকটিমের নাম, ছবি, ঠিকানা বা পারিবারিক পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই সংবাদের প্রচার এক ধরনের গুজব বা সামাজিক কলঙ্কের রূপ নিচ্ছে, যেখানে ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত পরিচয় হেয়প্রতিপন্ন করা হয়।
তাহলে প্রশ্ন ওঠে—এটি কি সাংবাদিকতা? নাকি সংবেদনশীলতাহীন গসিপ সংস্কৃতি?
সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও পেশাদারিত্বের অভাব- সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব হলো সত্য প্রকাশ করা, তবে সেটি অবশ্যই নৈতিক ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে করতে হবে। ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের সংবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সাংবাদিকতা নীতিমালায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে:
ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির নাম, ছবি বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।
ভিকটিমকে দোষারোপ বা লজ্জিত করে তোলার মতো কোনো তথ্য বা উপস্থাপনা গ্রহণযোগ্য নয়।
সংবাদের ভাষা হতে হবে সহানুভূতিশীল, আইনগত প্রক্রিয়াকে উৎসাহিতকারী ও অপরাধীর প্রতি কঠোর অবস্থানকারী।
কিন্তু বাস্তবে কি আমরা এই নিয়মগুলো মেনে চলতে দেখি? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সংবাদমাধ্যম শুধুমাত্র পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অতিরঞ্জিত শিরোনাম ব্যবহার করছে, যা ভিকটিমের জন্য মানসিকভাবে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।
ভিকটিম ব্লেমিং: সামাজিক অসচেতনতার প্রতিফলন- অনেক সময় ধর্ষণের সংবাদের ভঙ্গিমা এমন হয় যে সেখানে পরোক্ষভাবে ভিকটিমকেই দায়ী করার প্রবণতা দেখা যায়। কিছু গণমাধ্যম শিরোনামে এমন শব্দ ব্যবহার করে যা নির্যাতিত ব্যক্তির পোশাক, চলাফেরা বা সময়কে দায়ী করে তোলে। যেমন—
“রাতের অন্ধকারে একা বের হয়ে বিপদে পড়লো কিশোরী” “অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ালো তরুণী”
এ ধরনের উপস্থাপনা ভুক্তভোগীর প্রতি সহমর্মিতার বদলে সমাজের মধ্যে ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়ার এক অদ্ভুত মানসিকতা তৈরি করে। সাংবাদিকদের উচিত, ভাষার ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা এবং অপরাধীকে কাঠগড়ায় তুলে ধরার দিকে মনোযোগ দেওয়া।সামাজি যোগাযোগ মাধ্যম ও নৈতিক স্খলন- আজকাল ধর্ষণের সংবাদের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত নেতিবাচক। অনেক সময় পত্রপত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর ভুল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গুজব আরও বড় আকার ধারণ করে। কিছু ব্যক্তি ও সংবাদমাধ্যম ভিকটিমের ছবি ফেসবুক, টুইটার বা ইউটিউবে ছড়িয়ে দেয়, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অপরাধমূলক। বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির নাম ও ছবি প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তবুও অনেক সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এই আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে—এই ধরনের অপসাংবাদিকতার জন্য কি কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে?
অপরাধীর পরিচয় গোপন, ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ—কেন এই বৈপরীত্য? বাংলাদেশে আমরা প্রায়ই দেখি, ধর্ষকের নাম-পরিচয় গোপন রাখা হয়, অথচ ভিকটিমের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়। এমনকি ধর্ষকের পরিবারের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব থাকলে সংবাদ প্রকাশে ‘সংযম’ দেখানো হয়। এর ফলে অপরাধীরা সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু ভিকটিম আরও সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়।
আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা নীতিমালা ও বাংলাদেশের বাস্তবতা- জাতিসংঘ, রয়টার্স ফাউন্ডেশন, বিবিসি, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো ধর্ষণের সংবাদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করে:
ভিকটিমের অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।সংবাদের ভাষা হতে হবে সংবেদনশীল এবং বিচার ব্যবস্থাকে সমর্থনকারী।অপরাধীকে দায়ী করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, ভিকটিমকে নয়।কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে এসব নীতির প্রয়োগ খুব কম দেখা যায়।কি করা উচিত? সমাধানের পথ- ধর্ষণ সংবাদের অপব্যবহার রোধ করতে হলে সাংবাদিকদের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে। এজন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি: সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ: ধর্ষণের সংবাদের নৈতিক ও পেশাদারী দিক নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ: ধর্ষণের সংবাদের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করে সেটার কঠোর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অপরাধীদের পরিচয় উন্মোচন: ভিকটিম নয়, অপরাধী ও তার সহায়তাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করা উচিত। আইনের কঠোর প্রয়োগ: যারা ধর্ষণের ভিকটিমের তথ্য ফাঁস করে, তাদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও নারী নির্যাতন দমন আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। জনসচেতনতা বৃদ্ধি: পাঠক ও দর্শকদেরও বোঝানো দরকার যে, ধর্ষণ সংক্রান্ত সংবাদের দায়িত্বহীন উপস্থাপনা সমাজের ক্ষতি করছে।
সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়; এটি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। ধর্ষণের সংবাদের ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন রিপোর্টিং ভিকটিমের জন্য দ্বিতীয়বার মানসিক ধর্ষণের শামিল। তাই সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা অপরিহার্য।ধর্ষণ একটি ভয়াবহ অপরাধ। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ হলো, যখন এই অপরাধের শিকার ব্যক্তি গণমাধ্যমের ভুলের কারণে আরও লাঞ্ছিত হয়। তাই সাংবাদিকদের উচিত, সংবেদনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার মানদণ্ডে নিজেদের সাংবাদিকতাকে পরিচালিত করা। অন্যথায়, সাংবাদিকতার নামে আমরা শুধুমাত্র অন্যায়ের বৈধতা দিয়ে যাব। একটি রাষ্ট্রের শক্তি নির্ভর করে তার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতার ওপর। কিন্তু বাংলাদেশ আজ এক গভীর সংকটে, যেখানে সত্য বলার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে, আর সাংবাদিকতা পরিণত হয়েছে ক্ষমতার তোষামোদের যন্ত্রে। এই অবস্থা দেখে মনে হয়, আমরা এক ধর্ষিত সত্যের দেশে বাস করছি—যেখানে ন্যায়বিচারের আর্তনাদ রক্তের দাগ হয়ে সংবাদপত্রের পাতায় জমে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ কলমেই থাকে নির্লজ্জ নীরবতা। আমি প্রায় তিন দশক ধরে সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এই দীর্ঘ যাত্রায় পৃথিবীর ২৮টিরও বেশি দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, যেখানে সাংবাদিকতার প্রকৃত রূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকরা কীভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলেন—তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশে এর বিপরীত চিত্র। এখানে সাংবাদিকতার অনেকেই দায়িত্বশীলতা বোঝেন না, অনেকে বোঝেন, কিন্তু ভয় কিংবা স্বার্থের কারণে সত্য উচ্চারণ করেন না।
গণমাধ্যম: সত্যের রক্ষক নাকি ক্ষমতার দাস?
একসময় বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ছিল সাহসের আরেক নাম। কিন্তু এখন? অধিকাংশ সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল নির্লজ্জভাবে সরকারি প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং মিথ্যার মোড়কে জনগণকে ভুল পথে চালিত করা হয়। অনেক সাংবাদিক ক্ষমতার পদলেহন করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছেন।
যে দেশে সাংবাদিকের কাজ হওয়া উচিত সত্যকে সামনে আনা, সেখানে এখন অধিকাংশ সাংবাদিক পরিণত হয়েছেন ক্ষমতার বাহক বা ‘এজেন্ডা-সার্ভিস’-এর অংশীদার। যাঁরা সত্য বলেন, তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে মামলা, গ্রেপ্তার, নির্যাতন—এমনকি মৃত্যুও।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: আমাদের থেকে কত পিছিয়ে আমরা? বিদেশে, বিশেষত ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে সাংবাদিকরা কোনো ভয় ছাড়াই ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘ওয়াটারগেট’ কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়েছিল সাংবাদিকতার দুর্দান্ত এক নজির হিসেবে। সেই ঘটনার পর পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। অথচ আমাদের দেশে মন্ত্রী-এমপির দুর্নীতি প্রকাশ পেলেও কোনো জবাবদিহিতা নেই, বরং সংবাদকর্মীদের ওপরই চাপ বাড়ে।
জার্মানির বার্লিন, ব্রিটেনের লন্ডন, সুইডেনের স্টকহোম, কিংবা ফ্রান্সের প্যারিসে গিয়ে দেখেছি—সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করা সম্ভব নয়। কারণ সেখানে সাংবাদিকতা কেবল একটি পেশা নয়, বরং এটি একটি আন্দোলন, যা জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য লড়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ নিজেদের পেশাদারিত্ব বিসর্জন দিয়ে সুবিধাবাদী শিবিরে যোগ দিয়েছেন।
ভয়ের সংস্কৃতি ও সাংবাদিকদের আত্মসমর্পণ-
বাংলাদেশে সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় সংকট হলো ভয়। এখানে সত্য বলার জন্য সাংবাদিকদের হত্যা করা হয়, গুম করা হয়, মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে যাঁরা সত্য উচ্চারণ করেন, তাঁদের কণ্ঠরোধ করা হয়। সাংবাদিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে তাঁদের পরিবারকেও টার্গেট করা হয়।
এই ভয় এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতির কারণেই অনেক সাংবাদিক নিজেদের কলম বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁরা আজকাল আর সত্য বলেন না, বরং ক্ষমতার স্তুতি করেন। অনেকে নিরুপায়, আবার অনেকে স্বেচ্ছায় এই পথে গেছেন।
সমাধান কী? এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের রক্ষা করা, ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং সাংবাদিকতার নৈতিকতাকে পুনর্জীবিত করা।
আমাদের নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য এই বার্তা দিতে চাই—সাংবাদিকতা কখনোই কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নয়। এটি জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোর, রাষ্ট্রের ভুলত্রুটিগুলো সামনে আনার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাধ্যম।
বাংলাদেশে যদি সাংবাদিকতার এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা চলতে থাকে, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দরকার সাহসী, সত্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা, যারা ভয়কে জয় করে জনগণের পক্ষে দাঁড়াবেন। আর সেই দিনই বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে মুক্ত সাংবাদিকতার দেশ হবে।